হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট
দ্যা হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট (এইচজিপি) একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকল্প। এই প্রকল্পে মানুষের ডিএনএর নিউক্লিওটাইড বেইস পেয়ারের সিকোয়েন্স বের করার জন্য শুরু করা হয়। একই সাথে, দৈহিক এবং কার্যক্ষমের দিক থেকে সকল জিনের ম্যাপিং এবং তা সনাক্ত করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। [1] এখন অব্দি বিশ্বের সবচেয়ে বড় একসাথে দলগতভাবে করা জীববৈজ্ঞানিক প্রকল্প এটি।[2] ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এই ধারণা প্রথম নিয়ে আসলেও প্রকল্পটি সত্যিকার অর্থে শুরু হয় ১৯৯০ সালে এবং শেষ হয় ২০০০ সালে। দেশটির সরকার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) এর মাধ্যমে প্রকল্পটির অর্থায়ন করে। এছাড়াও বিশ্বজুড়ে একাধিক দল এই কাজে সম্পৃক্ত ছিল। একই সময়ে সেলেরা কর্পোরেশন, বর্তমানে সেলেরা জিনেটিক্স একই ধরনের প্রকল্পে হাত লাগায়, যা ১৯৯৮ সালে শুরু হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও জাপান, ফ্রান্স, জার্মানী, চীন ও কানাডার মোট ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রে এই প্রকল্পের কাজ চলে। [3]
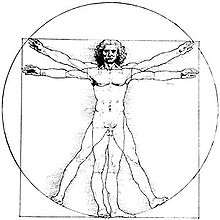
হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট
ইতিহাস
দ্য হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট একটি ১৫ বছরব্যাপী , সরকারি অর্থায়নে প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল ১৫ বছরের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ন ডিএনএ সিকুয়েন্স বের করা।[4] ১৯৮৫ সালের মে মাসে, রবার্ট সিনশাইমার একড়ি ওয়ার্কশপে মানুষের জিনোম সিকুয়েন্সিং করার আলোচনা করেন। [5] তবে একাধিক কারনে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ এই প্রকল্পে আগ্রহী ছিল না। একই বছরের মার্চে, সান্তা দে ওয়ার্কশপে চার্লস দেলিসি এবং ডেভিড স্মিথ এই ধারনাটি নিয়ে আলোচনা করেন।[6] একই সময় একটি বিজ্ঞান রচনায় রেনাটো ডুলবেকো সম্পূর্ন মানব জিনের সিকুয়েন্সিং এর কথা উল্লেখ করেন।[7] দুই মাস পরে জেমস ওয়াটসন কোল্ড স্প্রিং হারবর ল্যাবরেটরিতে এই ব্যাপারে একটি ওয়ার্কশপে পরিচালনা করেন।
ফলাফল
২০০১ সালের খসড়া ও ২০০৪ সালের পূর্ণাঙ্গ সিকুয়েন্স থেকে নিম্নোক্ত তথ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়ঃ
- অন্যান্য স্তন্যপায়ীর সাথে মানুষের প্রোটিন-কোডিং সংখ্যা মিলে। প্রায় ২২ হাজার ৩০০টি প্রোটিন কোডিং জিন মানুষের রয়েছে। [8]
- মানব জিন পূর্বের করা ধারণার চেয়েও বেশি একে অপরের সাথে মিলে বা আইডেন্টিকাল। [9][10][11]
- খসড়া প্রকাশিত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মেরুদন্ডী প্রাণীর জন্য নির্দিষ্ট ৭ শতাংশের চেয়েও কম প্রোটিন ফ্যামিলি এতে পাওয়া গেছে। [12]
অর্জন
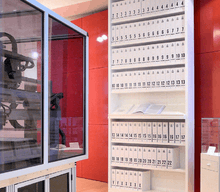
১৯৯০ সালে মানুষের জিনের তিন বিলিয়নের বেশি রাসায়নিক সাংগঠনিক উপাদানের বিন্যাস ও সনাক্তকরণের পদক্ষেপ হিসেবে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট শুরু করা হয়। এতে করে বিভিন্ন রোগের জিনেটিক মূল এবং এসব রোগের চিকিৎসা খুঁজে বের করার প্রয়াস চালানো যাওয়ার সুযোগ থাকে। মানুষের জিনোমে প্রায় ৩.৩বিলিয়ন বেইস-পেয়ার আছে, এটা বিবেচনায় নিয়ে এই প্রজেক্টকে একটি মেগাপ্রজেক্ট হিসেবে নেয়া হয়েছিল। জিনোম বিন্যাস হাতে আসার সাথে পরবর্তী ধাপ ছিল ঠিক কোন সব বিন্যাস সাধারণভাবে বহুল প্রচলিত রোগ যেমন বহুমূত্র বা ক্যান্সার হয় এবং এসবে চিকিৎসাপদ্ধতি বের করা। [13][14]
সেই আমলে প্রতিটি রোগীর আলাদা আলাদাভাবে জিন বিন্যাস করা অনেক খরচের ব্যাপার ছিল। তাও ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ একটি সহজ রাস্তা খুঁজে বের করে। তারা শুধুমাত্র সেসমস্ত অংশ খুঁজে বের করে যে অংশগুলোতে বেশিরভাগ ভিন্নতা রয়েছে। যেহেতু বেশিরভাগ প্রচলিত রোগই সাধারণ, তাই মনে করা হয়েছিল, জিনের সাধারণ অংশটুকুতেই এর এসব রোগের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। ২০০২ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ ইউরোপীয়ান, পশ্চিম এশিয়ান এবং আফ্রিকান মানুষের সাধারণ ভিন্নতা খুঁজে পেতে হ্যাপম্যাপ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে।[15]
সম্পূর্ণ মানবজিনোম প্রায় ১৫০,০০০ বেস-পেয়ার দৈর্ঘ্যে ছোট ছোট অংশে ভাঙ্গা হয়।[14] এই টুকরগুলো ব্যাক্টেরিয়াল কৃত্রিম ক্রোমোজোম ভেক্টর দ্বারা জোড়া লাগানো হয়। এই ব্যাক্টেরিয়াল কৃত্রিম ক্রোমজোম জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে নকশা করা হয়। এই ভেক্টর বহন করা ক্রোমোজমকে ব্যাক্টেরিয়ার প্রবেশ করা হয়। এতে ডিএনএ রেপ্লিকেশন পদ্ধতিতে ব্যাক্টেরিয়া জিনগুলোর কপি প্রস্তুত করে। এই সমস্ত ছোট ছোট টুকরোগুলো "শটগান" প্রজেক্টের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে সিকুএন্সিং করা হয় এবং সারিবদ্ধ করা হয়। [16][17]
সম্পূর্ন প্রজেক্টের খরচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার, মার্কিন যুক্তরাজ্যের একটি দাতব্য সংস্থা- দি ওয়েলকাম ট্রাস্ট এবং সারাবিশ্বের একাধিক সংস্থা বহন করে।[18][19]
জাতিসংঘের ইউনেস্কো বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণে দি হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে বিস্তর ভূমিকা রাখে। [20]
উন্নতি
প্রাপ্ত জিনোম ডাটার ব্যাখ্যা এবং গবেষণা এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই আছে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য চিকিৎসা ও জীবপ্রকৌশলীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। হিউম্যান জীনোম প্রজেক্ট সম্পূর্ণভাবে শেষ হোয়ার আগেই এরকম ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি পাওয়া গেছে। মাইরিয়াড জিনেটিক্সের মতো একটি কোম্পানি ইতিমধ্যেই জিনেটিক পরীক্ষা ব্যক্তগত পর্যায়ে শূরু করেছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন স্তন ক্যান্সার, যকৃতের অসুখ,তঞ্চন জটিলতা ইত্যাদির ঝুঁকি আগে থেকেই সনাক্ত করা যায়। এছাড়াও ক্যান্সার, আলঝেইমারের মতো রোগের কারণ খুঁজে পাওয়া সুযোগ অনেক উঁচু মাত্রায় বেড়ে গেছে। [15][21][22]
বিবর্তনের গবেষণায় বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএ সিকুয়েন্সিং নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিবর্তন সংক্রান্ত প্রশ্নে আণবিক জীববিজ্ঞান ফ্রেমে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া সম্ভব। রাইবোসম, বিভিন্ন অঙ্গাণুর উন্নতি, ভ্রুণের উন্নয়ন এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদির বিবর্তনীয় দিক নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ করে দেয়। [15][23]
উদাহরণস্বরূপ, ট্রিটিয়াম এস্টিভিয়ামের জিনেটিক গঠনের উপর করা গবেষনা থেকে গাছের বিবর্তনে গৃহস্থালীর প্রভাব নিয়ে গভীর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।[24] এরকম বিবর্তনের জন্য ঠিক কোন লোসাই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, এসব যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জিন সিকুয়েন্সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
নীতি, আইনগত এবং সামাজিক ইস্যু
মানব জিনোম প্রজেক্ট নিয়ে একাধিক নীতিগত, আইনত এবং সামাজিক দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে, জিনেটিক কোডের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টির একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। সবচেয়ে বেশি রকমের আশঙ্ককা করা হয় স্বাস্থ্য বীমা নিয়ে। মানুষের মাঝে এই আশঙ্কা জন্মে যে, জিন সংকেতের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট রোগের সম্ভাবনা থাকলে ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা বা এই সেবা থেকে বৈষম্য করার হার বেড়ে যাবে। [25] ১৯৯৬ সালে এই কারনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির নিজস্ব অনুমতি ছাড়া তাকে সনাক্ত করা যায় এরকম জিনগত তথ্য চিকিতসার্থে বা চিকিৎসাসেবা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত হস্তান্তর বা প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।[26] বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই প্রজেক্ট বিশাল অবদান রাখলেও কিছু লেখকের মতে, এই সিকুয়েন্সিং সামাজিকভাবে যে চাপ তৈরি করেছে তার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তাদের মতে, "রোগের আণবিক দিক তুলে ধরে চিকিৎসা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ার যে নতুন ধারণা তৈরি হয়েছে তা নতুন প্রজন্মের ডাক্তারদের প্রতি রোগীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তৈরি করে।[27]
তথ্যসূত্র
- Robert Krulwich (২০০১-০৪-১৭)। Cracking the Code of Life (Television Show)। PBS।
- "Economic Impact of the Human Genome Project – Battelle" (PDF)। সংগ্রহের তারিখ ১ আগস্ট ২০১৩।
- "Human Genome Project Completion: Frequently Asked Questions"। genome.gov।
- "Human Genome Project: Sequencing the Human Genome | Learn Science at Scitable"। www.nature.com। সংগ্রহের তারিখ ২০১৬-০১-২৫।
- Sinsheimer, Robert (১৯৮৯)। "The Santa Cruz Workshop, May 1985"। Genomics। 5: 954–956। doi:10.1016/0888-7543(89)90142-0।
- DeLisi, Charles (অক্টোবর ২০০৮)। "Conferences That Changed the World"। Nature। 455: 876–877। doi:10.1038/455876a। PMID 18923499। বিবকোড:2008Natur.455..876D।
- Dulbecco, Renato (১৯৮৬)। "Turning Point in Cancer Research, Sequencing the Human Genome"। Science। 231 (4742): 1055–1056। doi:10.1126/science.3945817। PMID 3945817। বিবকোড:1986Sci...231.1055D।
- Mihaela Pertea & Steven Salzberg (২০১০)। "Between a chicken and a grape: estimating the number of human genes"। Genome Biology। 11: 206। doi:10.1186/gb-2010-11-5-206। PMID 20441615। পিএমসি 2898077

- Venter, JC; ও অন্যান্য (২০০১)। "The sequence of the human genome"। Science। 291: 1304–1351। doi:10.1126/science.1058040। PMID 11181995। বিবকোড:2001Sci...291.1304V।
- International Human Genome Sequencing Consortium (IHGSC) (২০০৪)। "Finishing the euchromatic sequence of the human genome"। Nature। 431 (7011): 931–945। doi:10.1038/nature03001। PMID 15496913। বিবকোড:2004Natur.431..931H।
- Spencer, Geoff (২০ ডিসেম্বর ২০০৪)। "International Human Genome Sequencing Consortium Describes Finished Human Genome Sequence"। NIH Nes Release। National Institutes of Health।
- Bryant, J. A (২০০৭)। Design and information in biology: From molecules to systems। পৃষ্ঠা 108। আইএসবিএন 9781853128530।
...brought to light about 1200 protein families. Only 94 protein families, or 7%, appear to be vertebrate specific
- "About the Human Genome Project: What is the Human Genome Project"। The Human Genome Management Information System (HGMIS)। ২০১১-০৭-১৮। ২০১১-০৯-০২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১১-০৯-০২।
- Wellcome Sanger Institute। "The Human Genome Project: a new reality"। Wellcome Trust Sanger Institute, Genome Research Limited। ২০১৩-০৮-০১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১ আগস্ট ২০১৩।
- Naidoo N; Pawitan Y; Soong R; Cooper DN; Ku CS (২০১১)। "Human genetics and genomics a decade after the release of the draft sequence of the human genome"। Hum Genomics। 5 (6): 577–622। doi:10.1186/1479-7364-5-6-577। PMID 22155605। পিএমসি 3525251

- "Celera: A Unique Approach to Genome Sequencing"। ocf.berkeley.edu। Biocomputing। ২০০৬। সংগ্রহের তারিখ ১ আগস্ট ২০১৩।
- Davidson College (২০০২)। "Sequencing Whole Genomes: Hierarchical Shotgun Sequencing v. Shotgun Sequencing"। bio.davidson.edu। Department of Biology, Davidson College। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১ আগস্ট ২০১৩।
- Human Genome Information Archive। "About the Human Genome Project"। U.S. Department of Energy & Human Genome Project program। ২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১ আগস্ট ২০১৩।
- Human Genome Project Information Archive (২০১৩)। "U.S. & International HGP Research Sites"। U.S. Department of Energy & Human Genome Project। সংগ্রহের তারিখ ১ আগস্ট ২০১৩।
- Vizzini, Casimiro (মার্চ ১৯, ২০১৫)। "The Human Variome Project: Global Coordination in Data Sharing"। Science & Diplomacy। 4 (1)।
- Gonzaga-Jauregui C; Lupski JR; Gibbs RA (২০১২)। "Human genome sequencing in health and disease"। Annu Rev Med। 63 (1): 35–61। doi:10.1146/annurev-med-051010-162644। PMID 22248320। পিএমসি 3656720

- Snyder M, Du J; Gerstein M (২০১২)। "Personal genome sequencing: current approaches and challenges"। Genes Dev। 24 (5): 423–431। doi:10.1101/gad.1864110। PMID 20194435। পিএমসি 2827837

- Lander ES (২০১১)। "Initial impact of the sequencing of the human genome"। Nature। 470 (7333): 187–197। doi:10.1038/nature09792। PMID 21307931। বিবকোড:2011Natur.470..187L।
- Peng, J; Sun, E; Nevo, D (২০১১)। "Domestication Evolution, Genetics And Genomics In Wheat"। Molecular Breeding। 28 (3): 281–301। doi:10.1007/s11032-011-9608-4।
- Greely, Henry (১৯৯২)। The Code of Codes: Scientific and Social Issues in the Human Genome Project। Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press। পৃষ্ঠা 264–65। আইএসবিএন 0-674-13646-2।
- US Department of Health and Human Services। "Understanding Health Information Privacy"।
- Rheinberger, H.J. (২০০০)। Living and Working with the New Medical Technologies। Cambridge: Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 20।