কৃত্রিম উপগ্রহ
কৃত্রিম উপগ্রহ হলো মহাকাশে উৎক্ষেপিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত উপগ্রহ। [1]
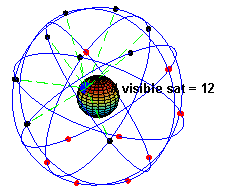
কিভাবে কাজ করে
কৃত্রিম উপগ্রহ এমনভাবে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান হয়, যাতে এর গতির সেন্ট্রিফিউগাল বা বহির্মুখীন শক্তি ওকে বাইরের দিকে গতি প্রদান করে - কিন্তু পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি একে পৃথিবীর আওতার বাইরে যেতে দেয় না। উভয় শক্তি কৃত্রিম উপগ্রহকে ভারসাম্য প্রদান করে এবং কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। যেহেতু মহাকাশে বায়ুর অস্তিত্ব নেই তাই এটি বাধাহীনভাবে পরিক্রমণ করে । কৃত্রিম উপগ্রহগুলো বৃত্তাকারে পরিক্রমণ করে না, তার গতি ডিম্বাকৃতির।
টিভি ও বেতারসংকেত প্রেরণ এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহগুলো সাধারণত পৃথিবীথেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে।
পৃথিবী থেকে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে তথ্য পাঠানো হয়, কৃত্রিম উপগ্রহ সেগুলো গ্রহণ করে এবং বিবর্ধিত (এমপ্লিফাই) করে পৃথিবীতে প্রেরণ করে । কৃত্রিম উপগ্রহ দুইটি ভিন্ন কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ব্যবহার করে সিগনাল (তথ্য) গ্রহণ এবং পাঠানোর জন্য । কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে আসা সিগনাল অনেক দুর্বল বা কম শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই প্রথমে ডিস এন্টেনা ব্যবহার করে সিগনালকে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং পরে রিসিভার দিয়ে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হয় ।
কৃত্রিম উপগ্রহের জ্বালানী
কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর উৎক্ষেপণের সময়ই পর্যাপ্ত জ্বালানি গ্রহণ করতে হয়।কারণ মহাকাশে রিফুয়েলিংয়ের কোনো সুযোগ নেই। তবে কিছু উপগ্রহ জ্বালানি হিসেবে সৌরশক্তি ব্যবহার করে। এদের গায়ে সৌরকোষ লাগানো থাকে, যা ব্যবহার করে থেকে সে সূর্য থেকে তার প্রয়োজনীয় শক্তি গ্রহণ করে । [2]
প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ
মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কৃতিত্ব সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর উৎক্ষেপিত স্পুটনিক ১ নামের কৃত্রিম উপগ্রহটির নকশা করেছিলেন সের্গেই করালিওভ[3] নামের একজন ইউক্রেনীয়। একই বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-২ উৎক্ষেপণ করে। স্পুটনিক-২ লাইকা[4] নামের একটা কুকুর বহন করে নিয়ে যায়। অবশ্য উৎক্ষেপণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে লাইকা মারা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর পরিকল্পনা করে। তাদের পরিকল্পনা সফল হয় ১৯৫৮ সালের ৩১ জানুয়ারি। তাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১ এদিন মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। ভারতের প্রথম মহাকাশ উপগ্রহ ASTROSAT
| ক্রমিক নং | দেশ | সাল | রকেটের নাম | উপগ্রহের নাম |
| ১। | ১৯৫৭ | স্পুটনিক-পিএস (রকেট) | স্পুটনিক-১ | |
| ২। | ১৯৫৮ | জুনো-১ | এক্সপ্লোরার-১ | |
| ৩। | ১৯৬৫ | ডায়ামান্ট | এস্ট.রিক্স | |
| ৪। | ১৯৭০ | ল্যাম্বডা-৪এস (রকেট) | ওসুমি | |
| ৫। | ১৯৭০ | লং মার্চ-১ | ডং ফ্যাং হং-১ | |
| ৬। | ১৯৭১ | ব্ল্যাক এ্যারো | প্রোসপেরো এক্স-৩ | |
| ৭। | ১৯৮০ | স্যাটেলাইট লাঞ্চ ভিহাইকেল (এসএলভি) | রোহিণী | |
| ৮। | ১৯৮৮ | শ্যভিত | ওফেক-১ | |
| ৯। | ১৯৯২ | সোয়ুজ-ইউ | কসমস-২১৭৫ | |
| ১০। | ১৯৯২ | সাইক্লোন-৩ | স্ট্রেলা | |
| ১১। | ২০০৯ | সাফির-২ | ওমিড | |
| ১২। | ২০১৮ | ফ্যালকন ৯ | বঙ্গবন্ধু-১ |
আবহাওয়া সংক্রান্ত কৃত্রিম উপগ্রহ
প্রথম আবহাওয়া সংক্রান্ত স্যাটেলাইট ভ্যানগার্ড-২[5] ১৯৫৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এটা আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাতে পারত। টাইরোস-১[6], তা ১৯৬০ সালের ১ এপ্রিল পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত হয় যা বিস্তারিতভাবে পৃথিবীর আবহাওয়া সংক্রান্ত ছবি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল । ওই বছরই ২৩ নভেম্বর টাইরোস-২ পৃথিবী থেকে বিচ্ছুরিত ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি পরিমাপ করে এবং আবহাওয়ার ছবিও সংগ্রহ করে। ১৯৬১ সালের ১২ জুলাই নিক্ষিপ্ত টাইরোস-৩ আটলান্টিক মহাসাগরের হারিকেন ইথার নামক ঝড় প্রথম আবিস্কার করে। এ ক্ষেত্রে হারিকেনের কারণে যেসব অঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে সেসব অঞ্চলকে আগেই সতর্ক করা হয়। এই ধারাবাহিক উপগ্রহমালার অনেক উপগ্রহ নিক্ষিপ্ত হয় যা তাপমাত্রা নির্ণয় করে মহাকাশে ইলেকট্রনের ঘনত্বের পরিমাপ করে। টাইরোস উপগ্রহমালার পর ঈসা এবং তারপর নিশ্বাস উপগ্রহমালা মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। ১৯৬৬ সালের ১৫ মে নিক্ষিপ্ত নিশ্বাস-২ উপগ্রহ পৃথিবীর উত্তাপের ভারসাম্য পরিমাপ করে। নিশ্বাস-১ হারিকেন ডেটার অনুসন্ধান দেয়। মানুষ জীবন ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য আবহাওয়া সংক্রান্ত স্যাটেলাইটগুলো হারিকেন, বন্যা ও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে আগেই সতর্কতা প্রদান করে থাকে। প্রায় সব স্যাটেলাইট মেঘের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করে। ম্যাগনেটিক টেপে সংবাদ জমা করে এবং তারপর টেলিমিটার দিয়ে গ্রাউন্ড স্টেশনে রক্ষিত কম্পিউটারে সোজাসুজি প্রেরণ করে। পৃথিবীর ওপর সেই সময় অবস্থানকারী মেঘের প্রণালীর ছবি পুনরুৎপাদনে সক্ষম হয়।
সংঘর্ষ ও ভূপাতিত
২০০৯ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ ইরিডিয়াম ৩৩ এবং রাশিয়ার কসমস ২২৫১ উপগ্রহের ধাক্কা লাগে। ঘটনাটি ঘটে সাইবেরিয়ার ৭৮৯ কিলোমিটার ওপরে। নাসা'র উপগ্রহ বিজ্ঞানি মার্ক ম্যাটনি এমএসএসবিসি চ্যানেল কে জানান[7], দুটি গোটা কৃত্রিম উপগ্রহের সম্মুখ সংঘাতের ঘটনা এই প্রথম ঘটল।[8]
মহাশুন্যের ব্ল্যাক হোল, নিউট্রন স্টারের ছবি তোলা, এক্স-রে ইত্যাদির উৎসস্থল খুঁজে বের করার জন্য ১৯৯০ সালে জার্মানির উপগ্রহ রোসাটকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মধ্যাকর্ষণজনিত কারণে বলয়ের মধ্যে চলে আসায় ২০১১ সালের ২২ কিংবা ২৩ অক্টোবরের মধ্যে এটি পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় আঘাত হানতে পারে বলে জার্মানির মহাকাশ কেন্দ্র ডিএলআর জানিয়েছে।[9]
ব্যবহার
মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে, বিশেষ করে কমিউনিকেশন (যোগাযোগ) এর কাজে স্যাটেলাইট অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় । বেশিরভাগ টেলিভিশন চ্যানেল তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে এর মাধ্যমে । তাছাড়া ইন্টারনেট সংযোগ, টেলিফোন সংযোগ, উড়ন্ত বিমানে নেটওয়ার্ক প্রদান, দুর্গম এলাকায় নেটওয়ার্ক প্রদান, জিপিএস সংযোগসহ বিভিন্ন কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহৃত হয় ।
তথ্যসূত্র
- বাংলা অভিধান
- কৃত্রিম উপগ্রহ
- এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা
- "Message from the First Dog in Space, Received 45 Years Too Late"। ৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১১ নভেম্বর ২০০৯।
- নাসার ওয়েব পৃষ্ঠা
- "স্মল স্যাটেলাইটস হোম পৃষ্ঠা"। ৬ জুলাই ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১১ নভেম্বর ২০০৯।
- এমএসএসবিসি চ্যানেল
- দ্য গার্ডিয়ান
- মহাকাশ থেকে আচমকা পতিত হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ, retrieved 24 October, 2011
বহিঃসংযোগ
- জে-ট্যাক থ্রী ডি এ থ্রী-ডাইমেনশন্যাল ডিসপ্লে অফ অল একটিভ স্যাটেলাইটস অরবিটিং প্ল্যানেট আর্থ
- স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড ট্র্যাকস
- 'আই-স ইন দ্য স্কাই' ফ্রি ভিডিও বাই ভেগা সায়েন্স ট্রাস্ট এণ্ড দ্য বিবিসি/ওইউ গত পঞ্চাশ বছরে কৃত্রিম উপগ্রহের বহুবিধ ব্যবহারের ইতিহাস
- হাউস্টাফ ওয়ার্কস কৃত্রিম উপগ্রহ কিভাএব কাজ করে
- UCS Satellite Database Lists operational satellites currently in orbit around the Earth. Updated quarterly.
- উৎক্ষেপণে বর্তমান ও অতীত ইতিহাস
- Satellite launch schedule